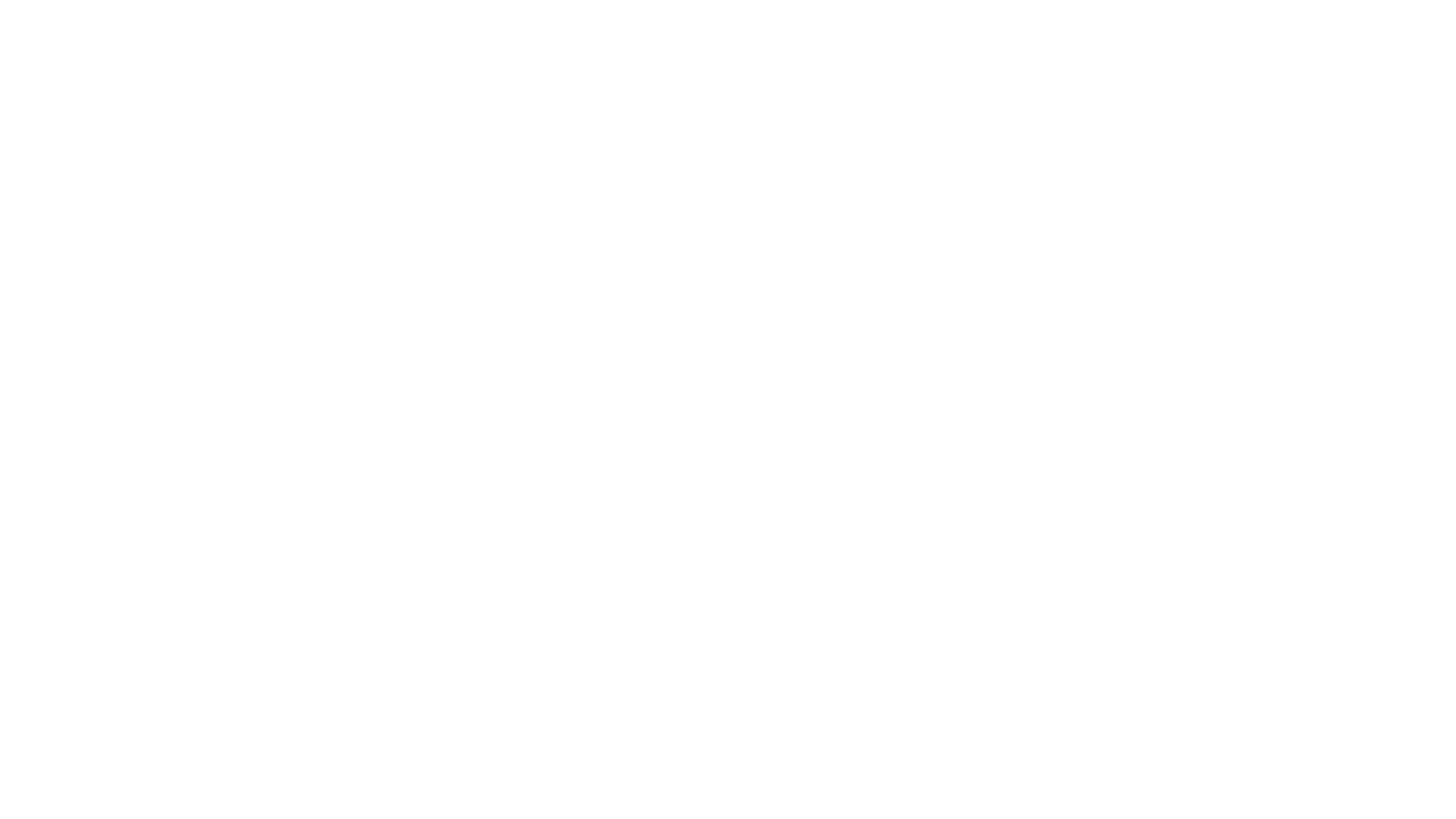
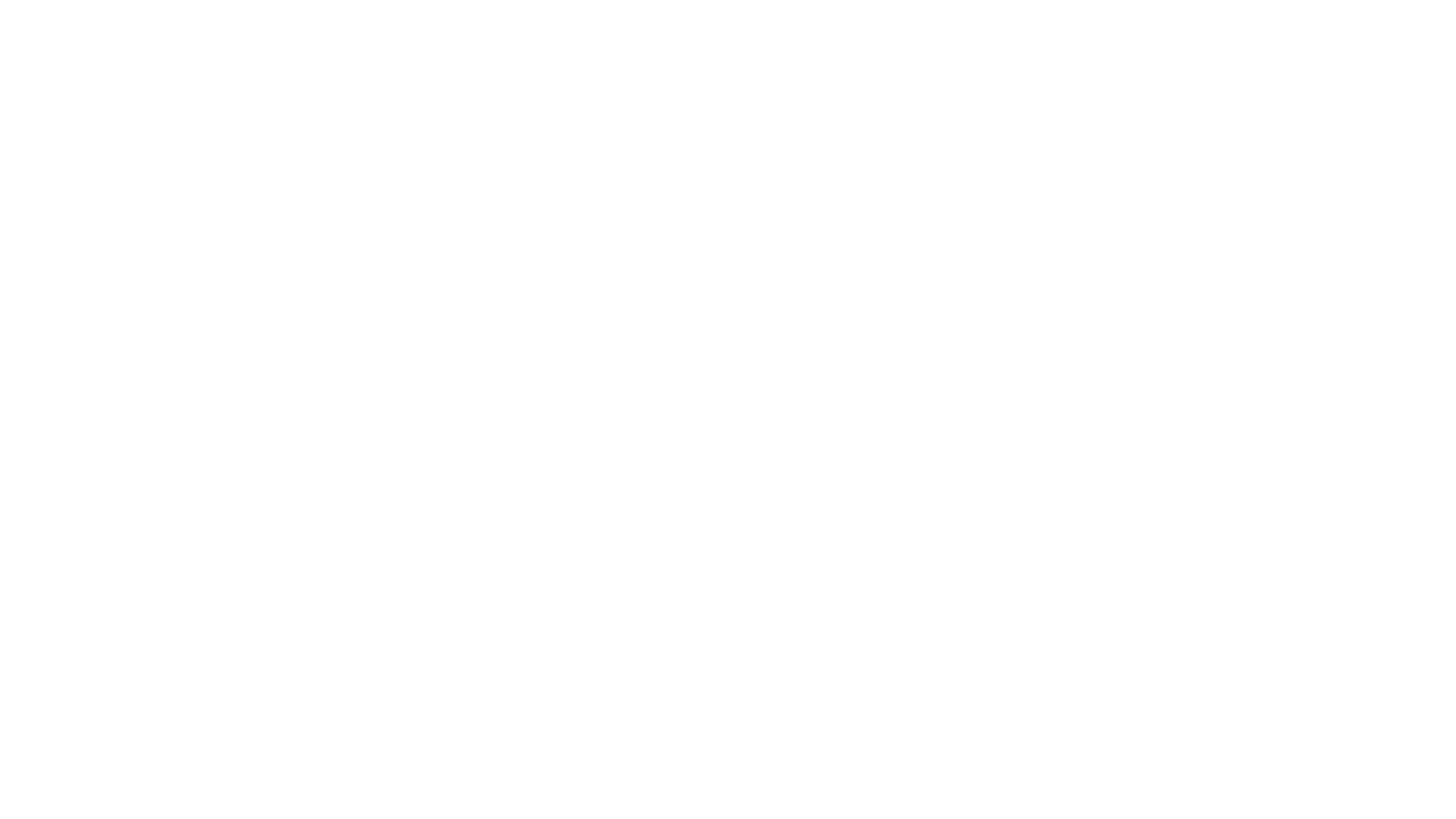
বাংলাদেশে দলিত ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সামাজিক মর্যাদা ও মানবাধিকারের প্রশ্নটি আমাদের জাতীয় বিবেকের সামনে এক কঠিন চ্যালেঞ্জ হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই জনগোষ্ঠী সামাজিক বঞ্চনা, জাতিগত বৈষম্য এবং অর্থনৈতিক নিপীড়নের শিকার। তাদের প্রতি ‘অস্পৃশ্যতা’ বা ‘অচ্ছুত’ ধারণা এখনো সমাজের গভীরে প্রোথিত, যা তাদের মৌলিক মানবাধিকার লাভে প্রধান অন্তরায়। বাংলাদেশের জনগোষ্ঠী যে বৈচিত্র্যময়, আমরা কি এই বৈচিত্র্যের শক্তি ধরে রাখতে পারছি? একশনএইড বাংলাদেশ, দীর্ঘ চার দশকের বেশি সময় ধরে প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করে আসছে এ অভিজ্ঞতারআলোকে, দলিত জনগোষ্ঠীর প্রতি বিদ্যমান বৈষম্য এবং এর সমাধানে একটি কার্যকর পথরেখা তুলে ধরা এ লেখার মূল উদ্দেশ্য।
‘দলিত’ শব্দটি সংস্কৃত এবং হিন্দি ভাষায় ‘ভগ্ন’ বা ‘ছিন্নভিন্ন’ অর্থে ব্যবহৃত হয়, যা নিপীড়িত ও অনগ্রসর জাতিগোষ্ঠীকে নির্দেশ করে। বাংলাদেশে এই জনগোষ্ঠী বিভিন্ন নামে পরিচিত, যেমন হরিজন, বেদে, ঋষি, মেথর, ধাঙড়, নাপিত, ধোপা, পাটনী, কামার, কুমার, জেলে, চামার ইত্যাদি; যাদের পেশা প্রায়ই সমাজের নিম্নস্তরের কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়। ব্রিটিশ আমলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, চা-বাগানের কাজ, পয়োনিষ্কাশন ইত্যাদি কাজের জন্য ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দরিদ্র দলিতদের এ দেশে আনা হয় এবং কাজের স্থানেই কলোনিতে তাদের থাকতে দেওয়া হয়।
বাংলাদেশে দলিত জনগোষ্ঠীর সঠিক পরিসংখ্যান নিয়ে ব্যাপক অস্পষ্টতা ও ভিন্নতা বিদ্যমান, যা তাদের জন্য কার্যকর নীতি প্রণয়নে একটি বড় বাধা। বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, এই সংখ্যা ৪৫ লাখ থেকে ৬৫ লাখ পর্যন্ত হতে পারে, এমনকি গণমাধ্যমের কোনো কোনো প্রতিবেদনে তা ৭৫ লাখও উল্লেখ করা হয়েছে। এই অস্পষ্টতা দলিতদের ‘অদৃশ্য’ করে রাখে, যা ‘কাউকে পেছনে ফেলে নয়’—টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) মূলনীতির পরিপন্থী। যদি সরকারের কাছে তাদের প্রকৃত সংখ্যা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকে, তাহলে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা বা আবাসনের মতো মৌলিক সুবিধাগুলো কীভাবে নিশ্চিত করা সম্ভব?
দলিত জনগোষ্ঠী সমাজে এখনো গভীর বৈষম্যের শিকার। তাদের অস্পৃশ্য মনে করার কারণে সব জায়গায় প্রবেশে বাধা, একই জায়গায় বসতে অনীহা, জমি বিক্রি না করা বা ঘরবাড়ি ভাড়া না দেওয়ার মতো ঘটনা নিত্যনৈমিত্তিক। ৩৮ শতাংশ দলিত হোটেল-রেস্তোরাঁয় খাবার খেতে গিয়ে সমস্যায় পড়ে। জন্ম ও জাতপাতের কারণে শত বছরের বঞ্চনা তাদের মধ্যে একধরনের বিচ্ছিন্নতার সংস্কৃতি জন্ম দিয়েছে।
অর্থনৈতিকভাবেও তারা চরম দুর্বল। মাত্র ৩৯ শতাংশ দলিত আয়মূলক নির্দিষ্ট কাজের সঙ্গে সংযুক্ত, যার বেশির ভাগই অপ্রাতিষ্ঠানিক ও অস্থায়ী। ৫৬ শতাংশ দলিত পরিবারের মাসিক আয় ৫ হাজার টাকার কম, যা দিয়ে মৌলিক চাহিদা মেটানো অসম্ভব। ৭৪ দশমিক ৭ শতাংশ দলিত ঋণগ্রস্ত, যাঁদের ৫৮ শতাংশ শুধু খাবারের খরচ মেটানোর জন্য ঋণ করেছেন। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও বিশ্বায়নের ফলে তাঁদের ঐতিহ্যবাহী পেশাগুলো সংকুচিত হচ্ছে, বাড়ছে বেকারত্ব।
শিক্ষাক্ষেত্রে দলিতদের অবস্থা উদ্বেগজনক। প্রায় ৬৩ শতাংশ দলিত শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ছে, যার প্রধান কারণ দারিদ্র্য ও জাতপাতভিত্তিক বৈষম্য। মাধ্যমিক পর্যায়ে দলিত শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণের হার মাত্র ১২ দশমিক ৫ শতাংশ, উচ্চশিক্ষায় ১ দশমিক ৯ শতাংশ। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তাদের প্রতি অবজ্ঞা ও বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়। একশনএইডের সহায়তায় দলিত সংস্থা কাজ করে দলিত শিশুদের উপবৃত্তিপ্রাপ্তি ও শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছে।
স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রেও দলিতরা পিছিয়ে। ৪৪ শতাংশ দলিত প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে যথাযথ চিকিৎসাসেবা নিতে পারেন না। দলিত ও আদিবাসী গর্ভবতী নারীদের টিকা ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা নিশ্চিত না করার দৃষ্টান্ত রয়েছে। ৭০ শতাংশ দলিত নারী স্বাস্থ্যসেবার সুবিধা পেতে সমস্যায় পড়েন। একজন দলিত নারীর গড় আয়ু ৪০ বছর, যেখানে উচ্চবর্ণের নারীদের আয়ু ৫৫ বছর, যা এক বিশাল বৈষম্য। ২৫-৪৯ বছর বয়সী ৫৬ শতাংশ দলিত নারী রক্তস্বল্পতায় ভোগেন। হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানেও অস্পৃশ্যতার চর্চা দেখা যায়।
দলিত নারীরা তিন স্তরে বৈষম্যের শিকার: দলিত হওয়ার কারণে, নারী হওয়ার কারণে এবং দুর্বল অর্থনৈতিক অবস্থার কারণে। জাতিগত পরিচয়ের কারণে তাঁরা অমানবিক কর্মপরিবেশ, মজুরিবৈষম্য ও যৌন হয়রানির সম্মুখীন হন। ৭৩ দশমিক ১ শতাংশ দলিত নারী গৃহিণী হিসেবে কাজ করেন। কারণ, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে তাঁদের ঘরের বাইরে যাওয়ার সুযোগ সীমিত।
পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা, যাঁদের অধিকাংশই দলিত, সমাজে অবহেলিত এবং তাঁদের সুযোগ-সুবিধা অনেক কম। তাঁদের বেতন অন্যান্য চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের তুলনায় নামমাত্র। পর্যাপ্ত সুরক্ষাসামগ্রীর অভাব, শোভন কর্মপরিবেশের অভাব, বিশ্রামাগারের অভাব এবং পুনর্বাসন ছাড়া উচ্ছেদের ভয় তাঁদের জীবনকে আরও দুর্বিষহ করে তোলে।
বাংলাদেশের সংবিধান সব নাগরিকের জন্য সমতা ও বৈষম্যহীনতার মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করে। অনুচ্ছেদ ২৭, ২৮, ২৯, ৩১, ৩২–সহ অন্যান্য ধারায় আইনের দৃষ্টিতে সমতা, ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী–পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে বৈষম্য নিষিদ্ধকরণ, সরকারি নিয়োগে সুযোগের সমতা এবং আইনের আশ্রয় লাভের অধিকারের কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশ জাতিসংঘের মানবাধিকার–সংশ্লিষ্ট প্রধান সনদগুলোকেও স্বীকৃতি দিয়েছে।
তবে সংবিধানের সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও বৈষম্য দূরীকরণের জন্য দেশে সুনির্দিষ্ট কোনো আইন নেই, যা আইনি প্রতিকার লাভে বাধা সৃষ্টি করে। ‘বৈষম্য বিলোপ আইন’ প্রণয়নের দাবি নিয়ে অনেক সংগঠন ২০০৭ সালে কাজ শুরু করে। ২০১৪ সালে আইন কমিশন এর খসড়া সুপারিশ করে। ২০১৮ সালে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন খসড়াটি পরিমার্জন করে মন্ত্রণালয়ে পাঠায়। অবশেষে ২০২২ সালে সংসদে ‘বৈষম্যবিরোধী বিল ২০২২’ উত্থাপন করা হয়। এই বিলের উদ্দেশ্য ছিল সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা ও মানবিক মর্যাদা নিশ্চিত করা।
কিন্তু দুঃখজনকভাবে, জাতীয় নির্বাচনের কারণে বিলটি আর আইন আকারে পাস হয়নি। নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে ‘বৈষম্য বিলোপ আইন’ করার দাবি জানানো হলেও উত্থাপিত আইনে ‘বিরোধী’ শব্দের অবতারণা করা হয়েছে। এ ছাড়া এই আইনে ‘দলিত’দের সংজ্ঞা নেই, যা থাকা উচিত বলে মনে করা হয়। এই দীর্ঘসূত্রতা ও শব্দগত পার্থক্য আইনের কার্যকারিতা ও এর চূড়ান্ত লক্ষ্যের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। নেপালে ২০১১ সালে ‘কাস্ট বেজড ডিসক্রিমিনেশন অ্যান্ড আনটাচেবিলিটি (অফেন্স অ্যান্ড পানিশমেন্ট) অ্যাক্ট’ প্রণীত হয়েছিল এবং তার বাস্তবায়নের জন্য একটি দলিত কমিশনও গঠিত হয়েছিল, যা বাংলাদেশের জন্য একটি দৃষ্টান্ত হতে পারে।
দলিত ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সামাজিক মর্যাদা ও মানবাধিকার নিশ্চিত করা কেবল তাদের মৌলিক অধিকার নয়; বরং বাংলাদেশের সামগ্রিক টেকসই উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। এ সমস্যার সমাধানে একটি সমন্বিত ও বহুমুখী পদ্ধতির প্রয়োজন। একশনএইড বাংলাদেশ, ফারাহ্ কবিরের নেতৃত্বে এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নিরন্তর অ্যাডভোকেসি ও মাঠপর্যায়ের কাজ করে যাচ্ছে।
১. আইনি ও নীতিগত সংস্কার:
• বৈষম্য বিলোপ আইন দ্রুত পাস: ‘বৈষম্যবিরোধী বিল ২০২২’–কে প্রয়োজনীয় সংশোধনসহ দ্রুত ‘বৈষম্য বিলোপ আইন’ হিসেবে পাস করা সময়ের দাবি। এই আইনে ‘দলিত’দের সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত করা এবং ‘বিলোপ’ শব্দটি ব্যবহার করা উচিত।
• দলিত কমিশন গঠন: দলিতদের অধিকার সুরক্ষা ও জীবনমান উন্নয়নে একটি স্থায়ী দলিত কমিশন গঠন করা জরুরি। কমিশনের প্রথম কাজ হবে দলিতদের ওপর একটি পূর্ণাঙ্গ শুমারি করা।
• সাংবিধানিক স্বীকৃতি: দলিতদের পরিচয়ের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা উচিত।
• শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্তিকরণ: পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত করা এবং তাঁদের কাজের নিশ্চয়তা ও নির্দিষ্ট বেতন স্কেল নিশ্চিত করা।
২. শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন:
• শিক্ষায় কোটা ও উপবৃত্তি: দলিত শিক্ষার্থীদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তিতে কোটা রাখা এবং উপবৃত্তি নিশ্চিত করা।
• কারিগরি প্রশিক্ষণ: দলিতদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান, যা তাঁদের জন্য নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে।
৩. স্বাস্থ্য ও জীবনমান উন্নয়ন:
• কমিউনিটি ক্লিনিক ও স্বাস্থ্যসেবা: দলিত পাড়াগুলোতে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন এবং বিশুদ্ধ পানি ও স্যানিটেশন–সুবিধার অপর্যাপ্ততা দূর করা।
• আবাসন ও পুনর্বাসন: ভূমিহীন দলিত জনগোষ্ঠীর জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে খাসজমির বন্দোবস্ত করা। পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের জন্য মহানগর ও পৌরসভায় আবাসনের ব্যবস্থা করা। পুনর্বাসন ছাড়া দলিত কলোনি/বসতি উচ্ছেদ নিষিদ্ধ করা।
৪. অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা:
• বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি: দলিতদের জন্য ‘সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি’র আওতায় বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা এবং এর কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।
• কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি: দলিতদের জন্য ঐতিহ্যগত পেশা সংকীর্ণ হওয়ায় নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
৫. সামাজিক অন্তর্ভুক্তি ও প্রতিনিধিত্ব:
• জনপরিসরে অভিগম্যতা: দলিতদের জনপরিসরে প্রবেশে বাধা প্রদানকারীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ।
• স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে প্রতিনিধিত্ব: স্থানীয় সরকার থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন কমিটিতে দলিত জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা। দলিত নারীদের নেতৃত্বে আনা এবং বাস্তবায়ন পর্যায়ে অংশগ্রহণের সুযোগ বাড়ানো।
• সচেতনতা বৃদ্ধি: বৈষম্য দূর করতে সমাজে সচেতনতা তৈরির কোনো বিকল্প নেই।
৬. তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণা:
• সঠিক পরিসংখ্যান: দলিত জনগোষ্ঠীর সঠিক জনসংখ্যা নির্ধারণে জরুরি ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা।
• পৃথক ডেটাবেজ: দলিত জনগোষ্ঠীকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা এবং তাদের জন্য একটি পৃথক ডেটাবেজ তৈরি করা।
বাংলাদেশে দলিত ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সামাজিক মর্যাদা ও মানবাধিকার নিশ্চিত করা কেবল তাদের মৌলিক অধিকার নয়; বরং দেশের সামগ্রিক টেকসই উন্নয়ন ও একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনের জন্য অপরিহার্য। সংবিধানের অঙ্গীকার ও আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতির পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।
জন্মগতভাবে প্রত্যেক মানুষ পূর্ণ মানবাধিকার ও সমমর্যাদার অধিকারী। প্রায় ৬৫ লাখ দলিত মানুষ, যার প্রায় অর্ধেকই নারী, জাতপাত ও পেশাগত পরিচয়ের কারণে নানাভাবে বৈষম্যের শিকার হন। এমন বঞ্চনার প্রতিকারে কোনো আইনি সুরক্ষা না থাকাটা গভীর উদ্বেগের বিষয়। এই জনগোষ্ঠীর প্রতি বিদ্যমান বহুমুখী বৈষম্য দূরীকরণে একটি সমন্বিত ও সুদূরপ্রসারী কৌশল গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। দলিত জনগোষ্ঠীর সঠিক পরিসংখ্যান সংগ্রহ এবং তাদের স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার মাধ্যমে তাদের ক্ষমতায়ন ও মূলধারায় অন্তর্ভুক্তি ত্বরান্বিত হবে। সর্বোপরি, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং অস্পৃশ্যতার মতো প্রথাগত বৈষম্য বিলোপে ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা অপরিহার্য।
একটি ন্যায়ভিত্তিক ও সমতাপূর্ণ বাংলাদেশ গড়ার পথে দলিত ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীদের কান্না শুনতে পাওয়া এবং তাদের অধিকার নিশ্চিত করা আমাদের সবার নৈতিক দায়িত্ব।
ফারাহ্ কবির কান্ট্রি ডিরেক্টর, একশনএইড বাংলাদেশ