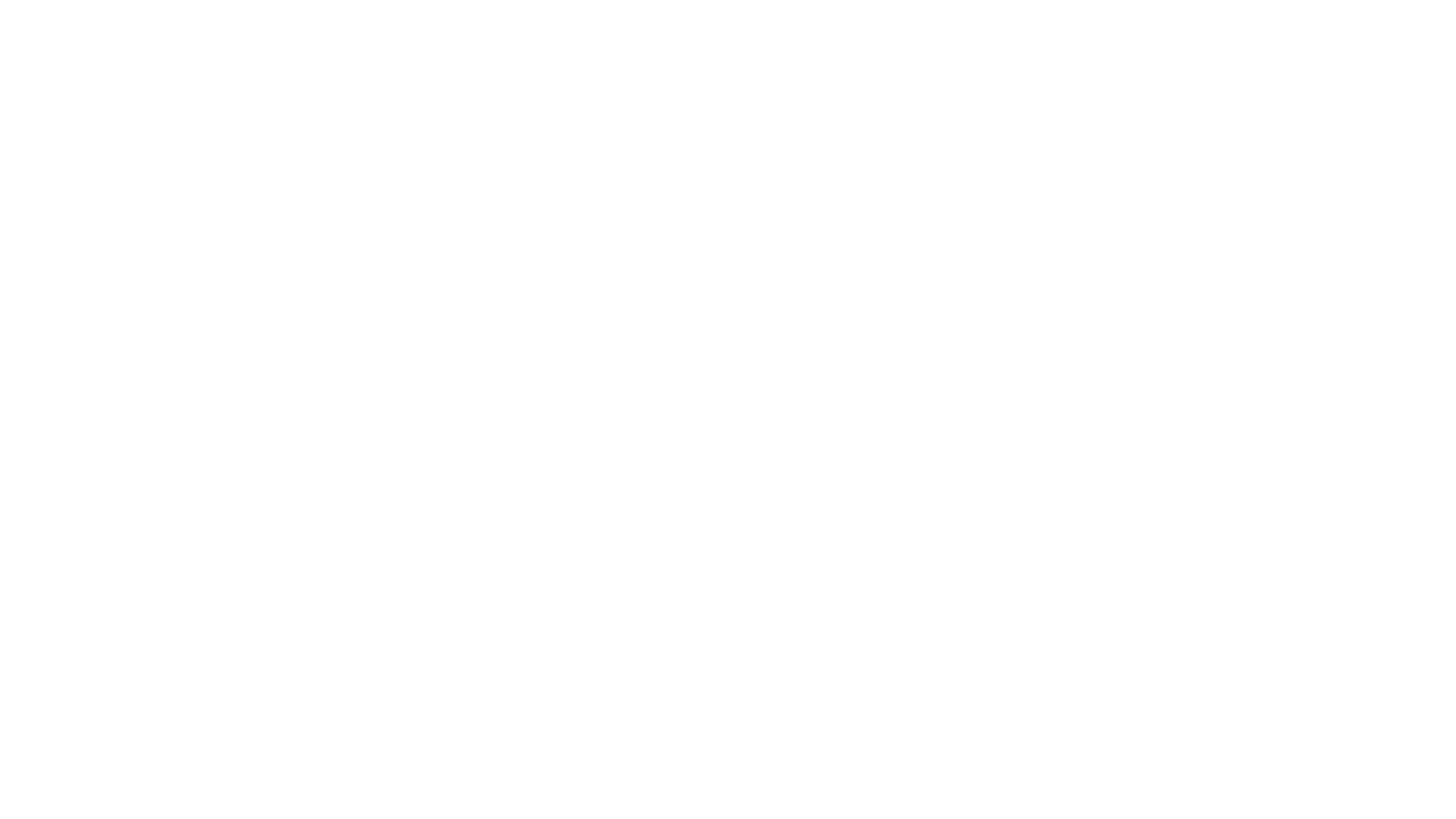
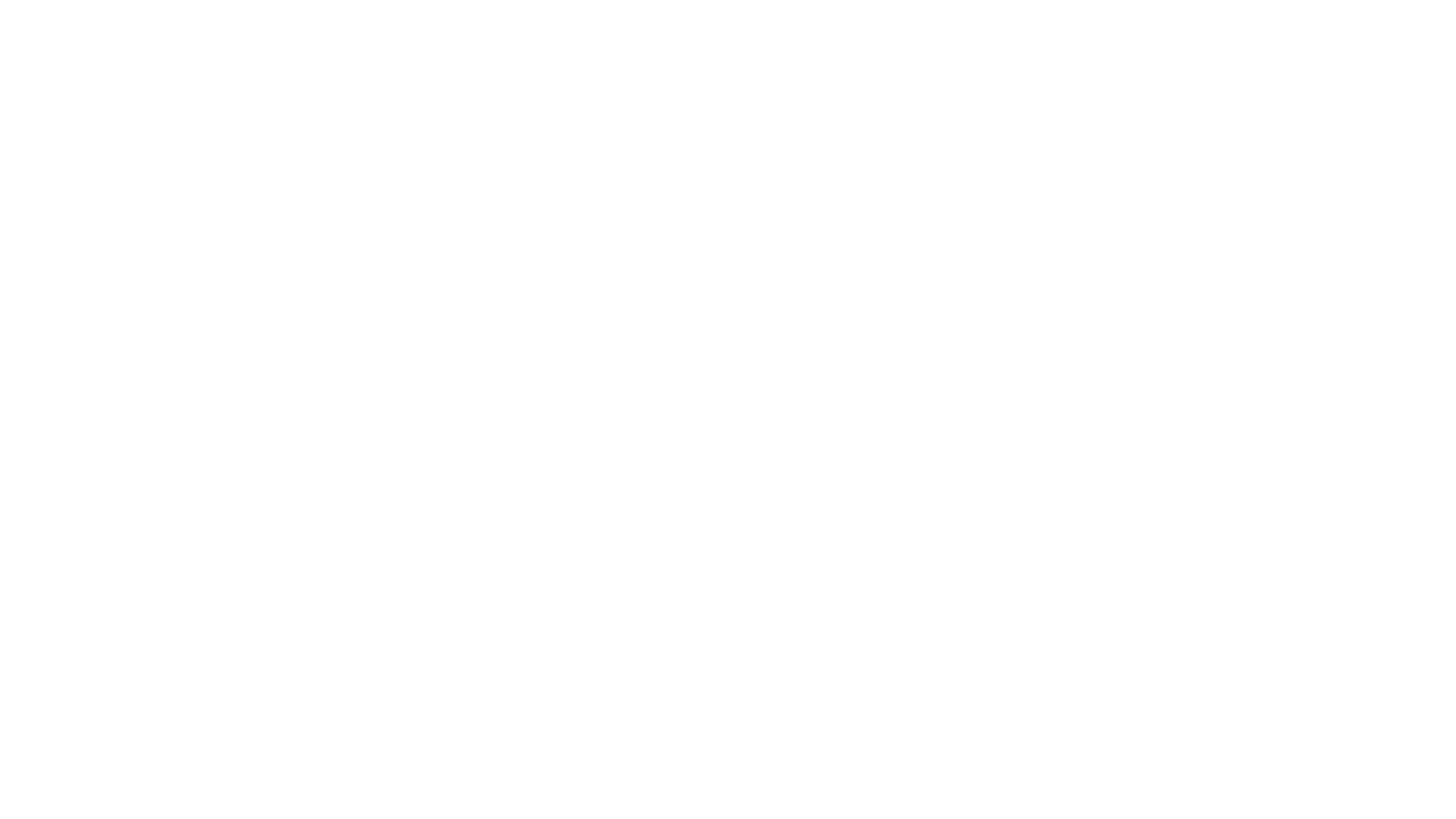
নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ও আসছে বাজেটের বাস্তবতা
এখন জাতীয় বাজেট প্রণয়নের চূড়ান্ত প্রস্তুতি চলছে। এবারের প্রস্তুতি এমন এক সময় যখন দেশের মানুষ নানা ধরনের অর্থনৈতিক চাপে আছে। বাজেট যেমন রাষ্ট্রের বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব তেমনি তা নাগরিকদের জীবনমান উন্নয়নের পথনির্দেশিকার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। বাজেট যেহেতু রাষ্ট্রের বাৎসরিক আর্থিক পরিকল্পনা তাই সমসাময়িক অর্থনৈতিক অবস্থা একে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। বাজেটে অর্থের সংস্থান হয় মূলত করের ওপর নির্ভর করে। কর আদায় ভালো হলে অর্থব্যয়ের জন্য রাষ্ট্রের কাছে যথেষ্ট সম্পদ থাকে। তবে কর আদায় ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান তলানিতে, ট্যাক্স জিডিপির অনুপাত মাত্র আট শতাংশ বা তার কম ফলে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রকে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের ওপর নির্ভর করতে হয়। এই ধরনের ঋণনির্ভরতা ইতিমধ্যে ঋণের দুষ্টচক্র তৈরি করেছে, যা ধীরে ধীরে আর্থিক স্বাধীনতার গণ্ডি সীমিত করে দিচ্ছে। আর এভাবে বর্তমান উন্নয়নের দায় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে গছিয়ে দেওয়া কতটুকু যৌক্তিক তা নিঃসন্দেহে একটি নৈতিক প্রশ্ন। এই সময়ের উন্নয়ন বাজেট পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এর পুরোটাই ঋণনির্ভর। আর পরবর্তী সময়ে এসব ঋণের সুদ পরিশোধ করতে গিয়ে রাষ্ট্রকে মৌলিক সেবাসমূহের ওপর বিনিয়োগ কাটছাঁট করতে হয়।
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের পর বিশ্বপরিস্থিতির যে টালমাটাল অবস্থা তা আমরা এখনো কাটিয়ে উঠতে পারিনি। মুদ্রাস্ফীতির পারদ যে চূড়ায় উঠেছিল তা নামার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। ডলারের বিপরীতে টাকার মান কমে যাওয়া এর একটি অন্যতম কারণ। প্রবাসীদের মাধ্যমে আয় বেড়েছে, আমদানি নিয়ন্ত্রণের কারণেও ডলারের দৃশ্যমান চাহিদা কমছে; তারপরও ডলারের ঘাটতি যেন কাটছেই না। অবশ্যই বিদেশি বিনিয়োগের মন্থরতা একটি বড় কারণ, সঙ্গে রয়েছে বৈদেশিক ঋণ ও দায় পরিশোধের চাপ। তবে অনেকেই এর পেছনে অবৈধ উপায়ে ডলার পাচারকে প্রধান কারণ মনে করেন। যদিও বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবি তাদের পর্যবেক্ষণের ফলে আমদানি ও রপ্তানিতে ওভার-ইনভয়েসিং ও আন্ডার-ইনভয়েসিং কমে এসেছে।
বাজেট এমন একটা ডকুমেন্ট যেখানে সরকারের আর্থিক নীতির প্রতিফলন হয়ে থাকে। এই বাজেট দেখেই নাগরিকরা আশান্বিত হন নয়তো তাদের হতাশায় নিমজ্জিত হতে হয়। সেই অর্থে এ বছরের বাজেট হতে পারে হতাশা কাটানোর বছর। বাজেটে জনগণের চোখ থাকে মূলত খাত অনুযায়ী বরাদ্দ ও কর ব্যবস্থাপনার ওপর। তবে এবারে তার থেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা। মুদ্রাস্ফীতির একটি কারণ যদি হয় বিশ্ব অর্থনীতির টালমাটাল অবস্থা আরেকটি বড় কারণ হচ্ছে অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার অভাব। বর্তমান অবস্থায় একমাত্র স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি এক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ফেরাতে পারে। আর তা নিশ্চিতে এবারের বাজেটে যদি সংস্কারের দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয় সেটাই হয়তো একটা পাওয়া। কারণ সাধারণের মতে বাজেটে বরাদ্দ যেটুকুই থাকুক না কেন বাস্তবায়নে তার প্রতিফলন কম। সম্পদের অপচয় অনেক বছর ধরে একটি বড় সমস্য। তবে এই মুহূর্তে বিশ্ব-অর্থনীতির টালমাটাল অবস্থা, মুদ্রাস্ফীতি এবং আসছে মধ্যম আয়ের দেশের স্বীকৃতির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বিনিয়োগকৃত সম্পদের কার্যকারিতা নিশ্চিত করাই এখন প্রধানতম উপায় বলে নাগরিকরা মনে করে।
সম্প্রতি এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ ও এর সহযোগী সংগঠনগুলোর উদ্যোগে বাজেটে নাগরিকদের মতামত জানতে একটি জরিপ পরিচালনা করা হয়। এই জরিপের ফলাফল অনুযায়ী বাজেটে বিবেচনার জন্য নাগরিকদের মধ্য থেকে যে ইস্যুগুলো উঠে আসে তার মধ্যে সবার আগে এসেছে শোভন কর্মসংস্থান (২১.৫৭ শতাংশ), শিক্ষা (১৭.৫১ শতাংশ), সামাজিক সুরক্ষা (১২.০৯ শতাংশ), অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ (৮.০৩ শতাংশ), দক্ষতা উন্নয়ন (৭.৬০ শতাংশ), নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য (৬.২৮ শতাংশ), কৃষি (৬.২৬ শতাংশ), নারীদের ক্ষমতায়ন (৬.১৯ শতাংশ), স্বাস্থ্য, শাসনব্যবস্থা, অবকাঠামো, শিক্ষা, আবাসন/পুনর্বাসন, জলবায়ু পরিবর্তন ইত্যাদি। পাশাপাশি এই জরিপে অংশগ্রহণকারী যুবারা যে অগ্রাধিকারের উল্লেখ করেছে তার মধ্যে রয়েছে কর্মসংস্থান (২৬.১১ শতাংশ), শিক্ষা (২৩.৩৩ শতাংশ), দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ (১৪.২৬ শতাংশ), এবং স্বাস্থ্যসেবা (৯.৪৪ শতাংশ)।
কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রায় সব বাজেটেরই একটি উদ্দেশ্য থাকে। তবে টেকসই শোভন কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য এখন শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করা প্রয়োজন। বেশ কয়েক বছর ধরেই বড়সড় আলোচনা হচ্ছে কারিগরি শিক্ষা নিয়ে। এ নিয়ে সরকারের বিনিয়োগও আছে তবে বেশিরভাগ বিনিয়োগ অবকাঠামোতে আটকে আছে। কারিগরি শিক্ষা বিস্তারের জন্য সরকার সারা দেশে উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মাণ করছে। কিন্তু অবকাঠামো নির্মাণ যে কর্মসূচির উদ্দেশ্য নিশ্চিত করতে পারে না তারা ভূরি ভূরি উদাহরণ এদেশে আছে। কারিগরি প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে সারা দেশের যুব উন্নয়নের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও কারিগরি প্রশিক্ষণগুলো কতটা কাজে লাগানো হয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন অজানা নয়। কারিগরি শিক্ষা বা প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বাজার উপযোগী কোর্সের প্রচলন ও মানসম্পন্ন শিখন পদ্ধতিই আসল। এখন বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার হওয়া উচিত সব ক্ষেত্রের বর্তমানের অবকাঠামোগুলোর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতের কর্মসূচি প্রণয়ন এবং তার জন্য বিনিয়োগ। তা যেমন শিক্ষাক্ষেত্রে প্রযোজ্য তেমনি অন্য ক্ষেত্রেও, বিশেষ করে স্বাস্থ্যে।
কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ যেমন সময়ের দাবি তেমনি সময়ের চাহিদা হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তি খাতের উন্নয়ন। সরকারের ইচ্ছাও তাই, ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে এক ধাপ বাড়িয়ে স্মার্ট বাংলাদেশ। তবে ডিজিটাল বাংলাদেশ ও স্মার্ট বাংলাদেশ তৈরির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক ডিজিটাল বিভক্তি ও দক্ষতার ঘাটতি। ডিজিটাল সাক্ষরতায় বিভক্তির পাশাপাশি বাংলাদেশে মাথাপিছু কম্পিউটারের ব্যবহার খুবই সীমিতি, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে ও মেয়েদের মধ্যে। এই সময়ে বৃহত্তর যুব সমাজের কাছে কম্পিউটার পৌঁছে দেওয়া ছাড়া সত্যিকারের বিভক্তি দূর করা যাবে না। বাজেটে ডিজিটাল বিভক্তি দূর করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার। পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যা মোকাবিলায় মানুষের বিপদাপন্নতা কমিয়ে আনা ও জীবন-জীবিকা নিশ্চিতকরণে বিশেষ বিবেচনা করা দরকার।
অন্যদিকে সমাজে ক্রমাগতভাবে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য বেড়ে যাওয়া এই সময়ে একটি বড় সমস্যা। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য কমানোর জন্য বাজেটে উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার। আর এই ধরনের কর্মসূচি শুধু সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলেই চলবে না, অধিকন্তু পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। একই সঙ্গে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন তখনই সম্ভব যখন সরকারি সেবার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা যাবে এবং তাদের জন্য কর্মসূচি প্রণয়ন করতে প্রগতিশীল কর কাঠামো প্রণয়ন করা হবে।
এবারের বাজেটে অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলার পাশাপাশি নতুন সরকারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের বিষয়টি গুরুত্ব বহন করে। নির্বাচনের আগে সরকারি দল আওয়ামী লীগ ‘স্মার্ট বাংলাদেশ : উন্নয়ন দৃশ্যমান, বাড়বে এবার কর্মসংস্থান’ এই স্লোগানে ইশতেহার ঘোষণা করে। এতে কর্মোপযোগী শিক্ষা ও যুবকদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা। বলা হয়েছে, অতিরিক্ত দেড় কোটি জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে এবং কর্মক্ষম, যোগ্য তরুণ ও যুবকদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণ, জেলা ও উপজেলায় ৩১ লাখ যুবকের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য সহায়তা প্রদান কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে। পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলা, দ্রব্যমূল্য ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে আসা, গণতান্ত্রিক চর্চার প্রসার, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর জবাবদিহি নিশ্চিত করা, ব্যাংকসহ আর্থিক খাতে দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি, নিম্ন আয়ের মানুষদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা সুলভ করাসহ মোট ১১টি বিষয়ে বিশেষ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও এতে ২০৩১ সালের মধ্যে দেশকে উচ্চ-মধ্যম আয়ের কাতারে নিয়ে যাওয়া এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে। নির্বাচনের প্রতিশ্রুতির মধ্যে আরও ছিল রাষ্ট্র পরিচালনার সব ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, সুশাসন ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চা সুদৃঢ় করা। আর্থিক খাতে এটাই এখন বেশি দরকার।
সার্বিক পরিস্থিতি বলছে সরকারি দলের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ও বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি যেন বিপরীতমুখী অবস্থানে আছে। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের দিকনির্দেশনা এবারের বাজেটের জন্য সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শুধু নির্দেশনাই যথেষ্ট না, নির্দেশনা বাস্তবায়নে বিশ্বাসযোগ্য পথরেখা লাগবে। কারণ প্রতিশ্রুতির কোনো কমতি নেই কিন্তু বাস্তব ও কার্যকর উদ্যোগের অভাবে সেই প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন করা যায় না। ফলে প্রান্তিক জনগণের কোনো পরিবর্তন হয় না, ধনী ও দরিদ্রদের মধ্যে বৈষম্য ও পার্থক্য কমে না। সরকারের প্রতিশ্রুতি আছে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করে দুর্নীতিকে মোকাবিলা করার। এবার দেখার বিষয় এবারের বাজেট সেই প্রতিশ্রুতি ধারণ করতে পারে কি না; পারলেও সেটাই বা কতটা আর না পারলেও সেটা কতটা।
লেখক: উন্নয়নকর্মী ও কলামিস্ট
psmiraz@yahoo.com