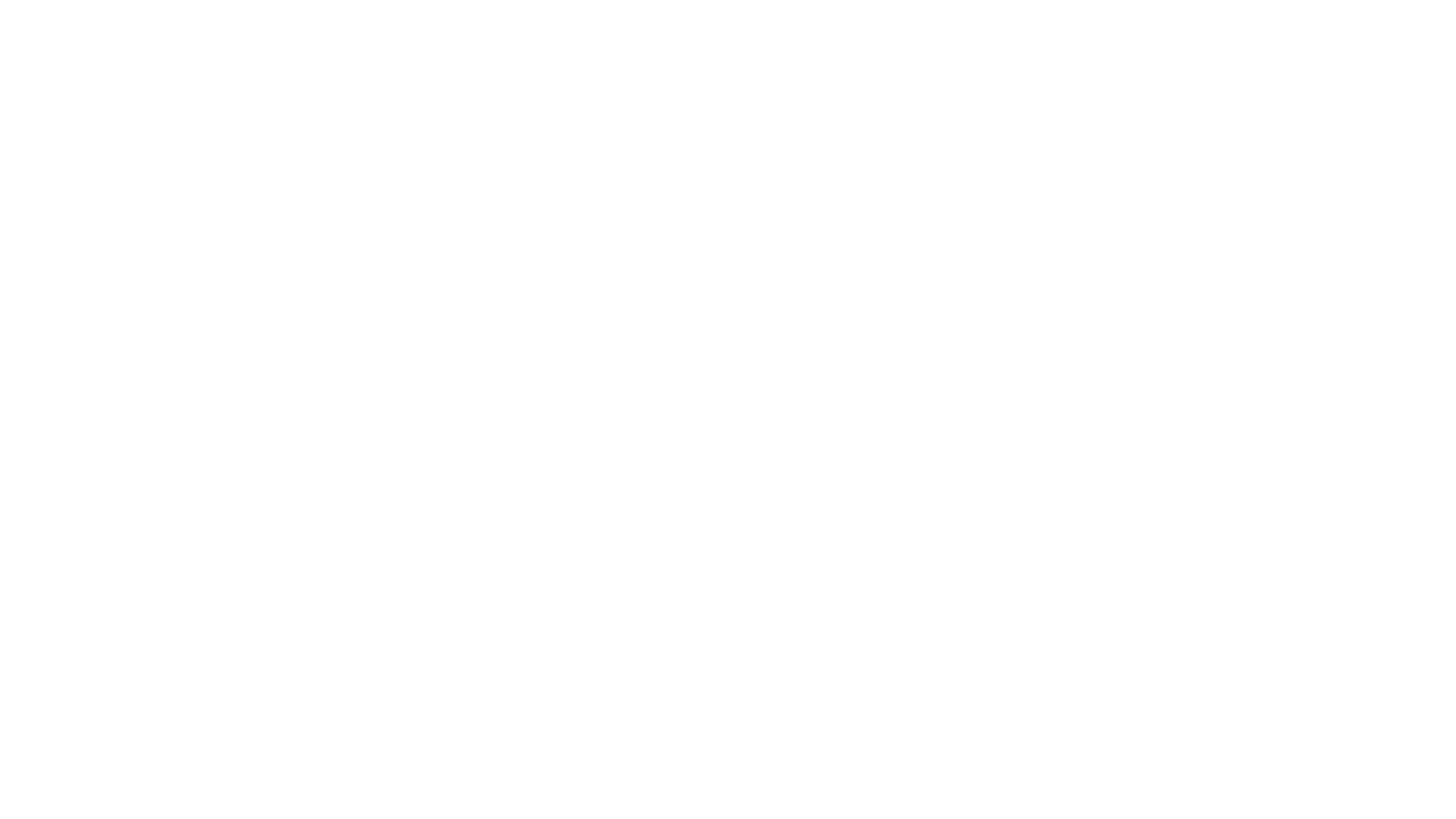
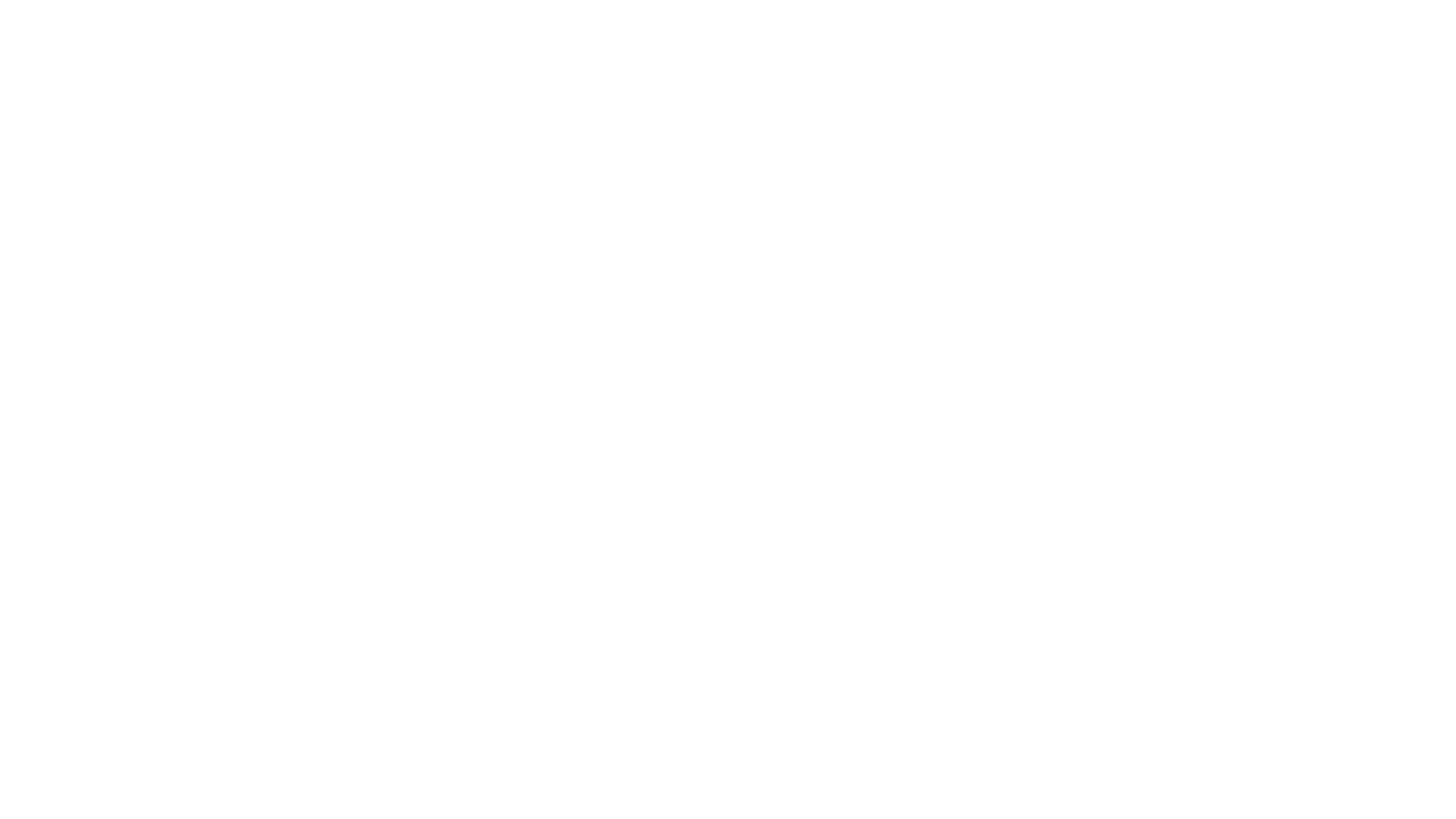
নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়ার সংস্কৃতি
স্মার্ট ও উন্নয়নশীল বাংলাদেশ গড়ার জন্য চাই স্মার্ট গভর্নেন্স। যদিও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার জন্য সরকারের প্রতিশ্রুতি স্মার্ট গভর্মেন্ট। গভর্নেন্সের মূল বিষয় পরিচালনা ব্যবস্থা যাকে আবার নিয়ন্ত্রণ করে কিছু কাঠামো, নীতি, সংস্কৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গি। আর এসবের পরিবর্তন না হলে স্মার্ট তো দূরের কথা গভর্নেন্স উন্নয়নশীল দেশের উপযোগী হয়ে উঠবে না বলাই বাহুল্য। উন্নয়নশীল বিশ্বে পদার্পণ করাই হয়তো এই মুহূর্তের বড় চ্যালেঞ্জ। শুধু ঝুঁকি মোকাবিলায় নয় বরং বিশ্বের সঙ্গে তাল মেলাতে, বাংলাদেশের সম্ভাবনার দুয়ার উন্মোচন করতে মোটকথা টেকসই অর্থনীতি ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে। আর তা করতে না পারাই হচ্ছে প্রথমত সম্ভাবনার অপমৃত্যু, পাশাপাশি জীবন ও সম্পদের ধ্বংস। ঢাকায় একের পর এক অগ্নিকাণ্ড, তার মাধ্যমে প্রাণ ও জীবনের ক্ষয় যেন তারই প্রতিফলন।
সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দেশের বিশেষ করে শহরাঞ্চলগুলোর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বেড়েছে বহুগুণ। কিন্তু ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তেমন দৃশ্যমান উন্নতি হয়নি। সেক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় প্রয়োজনীয় মানদণ্ড মেনে চলার ঘাটতিই যথেষ্ট কিছুদিন পরপর এভাবে একটি ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ডের মতো ঘটনা ঘটার জন্য। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য মতে গত ১৪ বছরে এভাবে অগ্নিকাণ্ডে নিহত মানুষের সংখ্যা ২ হাজার ৫০০ এর বেশি।
এবারের অগ্নিকাণ্ডের পর ঢাকার বিভিন্ন অঞ্চলে রেস্টুরেন্টের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দপ্তরের পক্ষ থেকে যে অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে তা বেআইনি না হলেও কিছুটা যে অতিরঞ্জন এখানে নেই তা বলা যাবে না। এসব অভিযান জনপ্রিয় হলেও এর অনেকটাই ঘটনার আগের নিষ্ক্রিয়তার দায় এড়ানোর চেষ্টা। এর আগে যে দু’একটি উদ্যোগ চোখে পড়ে তার বিপক্ষে প্রবল প্রতিরোধ তৈরি হয় তথাকথিত সুবিধাভোগীদের পক্ষ থেকে। বেইলি রোডের এত বড় ঘটনার পরও এই সুবিধাভোগীদের এখনো সক্রিয় দেখা যায়। আর এই সুবিধাভোগীরা হচ্ছে মূলত ব্যবসায়ী শ্রেণি বা মালিক পক্ষ যারা আবার রাজনৈতিকভাবেও ক্ষমতাবান। বেইলি রোডের অগ্নিকাণ্ডের পরে জানা যায়, এই বিল্ডিং ঝুঁকি বিবেচনায় তিন বার নোটিস প্রদান করা হয়েছিল কিন্তু সেখানেই শেষ। প্রশ্ন করাই যায়, নোটিস প্রতিপালনের ব্যর্থতার পরবর্তী ধাপ কী? এরকম কতগুলো বাণিজ্যিক স্থাপনা বন্ধ করা হয়েছে? সাবেক গণপূর্তমন্ত্রী সম্প্রতি সংসদে জানিয়েছেন এরকম ১৩০০ ঝুঁকিপূর্ণ ভবন চিহ্নিত করা হয়েছিল। আমাদের দেশের রাজনৈতিক বাস্তবতায় এসব ভবনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া বা বন্ধ করে দেওয়াটা কতটা সম্ভব সে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। যে কয়েকটি শক্ত পদক্ষেপ এখন পর্যন্ত গ্রহণ করার হয়েছে সেগুলোর বেশিরভাগই সর্বোচ্চ রাজনৈতিক সমর্থনপুষ্ট হতে হয়েছে। কিন্তু এর বাইরে সবকিছুই যেন অব্যবস্থাপনার চূড়ান্ত।
এ দেশের রাজনৈতিক বাস্তবতায় সবকিছুতেই প্রয়োজনীয় মানদণ্ড অনুসরণ করা খুবই কঠিন। তা শুধু একটি গোষ্ঠীকে তুষ্ট করার জন্য বা তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যই না। সমালোচকরা বলেন এর পেছনে মূল ভূমিকা হচ্ছে দুর্নীতির সুযোগ খোঁজা। আর এর প্রভাবেই আবাসিক ভবন বাণিজ্যিক হয়ে যায় কোনো ধরনের মানদণ্ড বজায় রাখা ছাড়াই। আবার এই বাণিজ্যিক ভবনগুলো কোনো কোনোটি বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত, এবং সেভাবেই চলতে থাকে কোনো একটি বড় দুর্ঘটনা ঘটার আগ পর্যন্ত।
ঢাকায় বেশিরভাগ ভবনেই অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নেই। থাকলেও তা মেয়াদ উত্তীর্ণ, প্রয়োজনে কোনো কাজে লাগে না। অন্যদিকে জরুরি অগ্নিনির্বাপণ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল ও প্রস্তুতি দুটোরই ঘাটতি চোখে পড়ার মতো। এই ভবনগুলোর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এমন অবস্থা থাকে যে এতে পরিস্থিতি তৈরি হয়েই থাকে, শুধু মাত্র ছোট একটি বিস্ফোরণের অপেক্ষা। আর একবার হওয়ার পরে কোনো ধরনের প্রতিরোধ ব্যবস্থা এসব ক্ষেত্রে কাজ করে না। তখন ‘ভবনে কোনো ধরনের অগ্নিনির্বাপণের ব্যবস্থা ছিল না’ এই ধরনের যুক্তি শুধু দায়িত্বশীলদের দায়িত্ব এড়ানোর একটি প্রচেষ্টা হতে পারে।
সময়ের সঙ্গে আমাদের আর্থসামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে। এই পরিবর্তনের সঙ্গে ব্যবস্থাপনার পরিবর্তন হচ্ছে না। সমাজের পরিবর্তন যত দ্রুত হচ্ছে তার সঙ্গে শাসনব্যবস্থার সামগ্রিক কাঠামো খাপ খাওয়াতে পারছে না। অনেক সময় কী করতে হবে তা নিয়ে যেন খেই হারিয়ে ফেলছে। একদিকে প্রয়োজনের চাহিদা মেটাতে পারছে না, অধিকন্তু পুরনো অবস্থা টিকিয়ে রাখতে যারপরনাই ব্যস্ত ওই সুবিধাভোগী একটি গোষ্ঠী। আবার এর মধ্যে রয়েছে এক সংস্থার সঙ্গে আরেক সংস্থার রশি টানাটানি।
গত কয়েক দশকে যদি ঢাকা ও আশপাশের অগ্নিকাণ্ডের চিত্র দেখি এর বেশিরভাগই ঘটেছে নতুন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে। গার্মেন্টস, রাসায়নিক গুদাম, কারখানা, হোটেল রেস্টুরেন্টে এমনসব অগ্নিকা-ের ঘটনাই ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের নির্দেশ প্রদান করে। এসব ঘটনার মধ্যে গত কয়েক বছরের উদ্যোগের ফলে গার্মেন্টস কারখানায় অগ্নিকাণ্ড দৃশ্যত অনেকটা নিয়ন্ত্রণে এসেছে। ক্রেতাদের চাপে গার্মেন্টস কারখানাগুলোকে তৃতীয় পক্ষের সহযোগিতা নিতে হয়েছে। এজন্য গার্মেন্টস মালিকদের কারখানাগুলো নিরাপদ করতে বিনিয়োগ করতে হয়েছে। সেই সময় মালিকরা যদিও এর বিপক্ষে ছিলেন কিন্তু তার সুফল এখন দেখা যাচ্ছে। তবে গার্মেন্টস ছাড়া অন্য সেক্টরগুলোতে দৃশ্যমান কোনো অগ্রগতি হয়নি। মূলত প্রশাসনের জায়গা থেকে যে দিকনির্দেশনা ও কঠোরতা প্রয়োগ করার প্রয়োজন ছিল তার কোনোটাই দেখা যায়নি। অধিকন্তু মানুষের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এক ধরনের ছাড় দেওয়ার সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে। মূলত রাজনৈতিক ও ক্ষমতাবানদের মদদপুষ্ট হয়ে কেবল মুনাফার জন্য তারা নিরাপত্তার প্রশ্নে নানা ধরনের যুক্তি তৈরি করে। যা শেষ পর্যন্ত বিশৃঙ্খলার সংস্কৃতি তৈরি করছে প্রায় সব ক্ষেত্রেই। এই বিশৃঙ্খল অবস্থা নিয়েই প্রতিনিয়তই নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছি। কিন্তু প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিটুকু গ্রহণ করছি না। এখনই যদি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা না যায় তবে এ ধরনের ঘটনা আরও ঘটবে। এবং একটি বিশৃঙ্খল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এই ধরনের দুর্ঘটনা যে অস্বাভাবিক নয় তা অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা থেকে বোঝাও কোনোভাবেই কঠিন না।
আমাদের দেশের অর্থনীতির পরিকল্পনায় ঝুঁকি মোকাবিলার পরিকল্পনা কতটুকু থাকে তা প্রশ্ন সাপেক্ষে। তার পরেও যতটুকু থাকে তাও আবার অর্থনৈতিক ঝুঁকি সম্পর্কিত, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কর, আর্থিক প্রণোদনা ও বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কিত। কিন্তু এই পরিকল্পনা দুর্ঘটনা সম্পর্কিত ঝুঁকিসমূহ বিবেচনায় নেওয়ার কোনো দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। এখন পর্যন্ত একের পর এক ঘটনার মধ্য দিয়ে নোটিস দেওয়ার ব্যবস্থা হয়তো তৈরি হয়েছে কিন্তু বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি কোনো। অভিযোগ আছে প্রশাসনের লালফিতার দৌরাত্ম্য এমন যে এর মূল উদ্দেশ্যই থাকে সেবাগ্রহণকারীদের টেবিলে টেবিলে ঘোরানো। এর পেছনে থাকে ঘুষের সংস্কৃতি। অর্থনৈতিক উদ্যোগে সহযোগিতা করা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা বাজায় রাখার ক্ষেত্রে প্রশাসন কতটুকু সহায়ক তা বলা মুশকিল। আবার অতীতের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে প্রশাসন ব্যবসায়ীদের দাবি-দাওয়া ও তাদের যুক্তির প্রতি যতটা সংবেদনশীল ততটা আগ্রহী নয় সাধারণ জনগণের জান ও মালের প্রতি, তাদের দাবি-দাওয়ার প্রতি।
এখন প্রশ্ন হচ্ছে একের পর এক ঘটনার মধ্য দিয়ে বিশ্বের সামনে আমাদের যে পরিচয় গড়ে উঠছে তা মধ্যম আয়ের অর্থনীতির জন্য কতটুকু সহায়ক? তবে এই অবস্থার জন্য শুধু প্রশাসনিক উদ্যোগই দায়ী না, এর জন্য রাজনৈতিক নেতৃত্বের ব্যর্থতাও কোনো অংশে কম না। রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রশাসন ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর কাছে একদিকে দৃঢ় অবস্থান ধরে রাখতে পারছে না, পাশাপাশি প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের ঘাটতিও রয়েছে। তবে তার থেকেও বড় প্রশ্ন, এর ধারাবাহিকতা আর কতদিন চলবে? শুধু মাথাপিছু আয় দিয়েই আমরা মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হব? আমরা স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে শুধু দুর্যোগ মোকাবিলার ক্ষেত্রেই না, এর বাইরেও আরও নতুন নতুন সমস্যা মোকাবিলা করার পূর্বপ্রস্তুতি থাকতে হবে। আর এজন্য নতুন সক্ষমতার পাশাপাশি প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। মনে রাখা দরকার ঔপনিবেশিক সময়ের মতো প্রশাসনিক উদ্যোগ শুধু জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করা না, অধিকন্তু জনগণের অধিকারের সুরক্ষা দেওয়া, অধিকার আদায়ের নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরি করাও এর বড় দায়িত্ব। নতুন অর্থনীতি কিছু ব্যবস্থাপনাগত সংকট যেমন তৈরি করছে একই সঙ্গে কিছু সুযোগও তৈরি করেছে। তাই অর্থনৈতিক উন্নয়নকে টেকসই করার জন্য সেই সুযোগকে কাজে লাগানো দরকার এবং তা সম্ভব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনাগত পরিবর্তনের মাধ্যমে।
লেখক: উন্নয়নকর্মী ও কলামিস্ট
psmiraz@yahoo.com